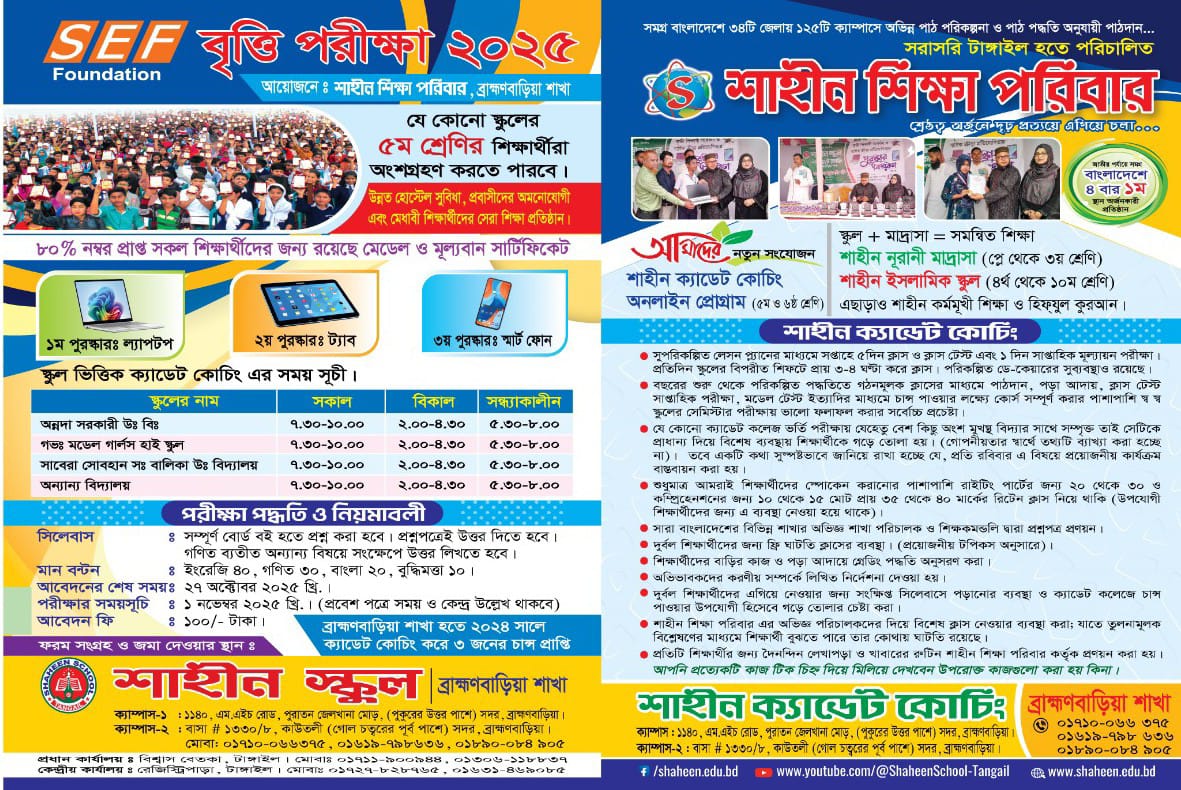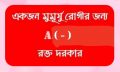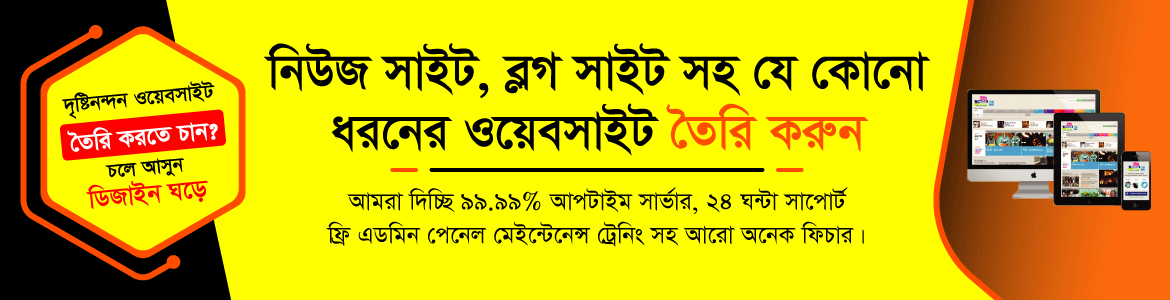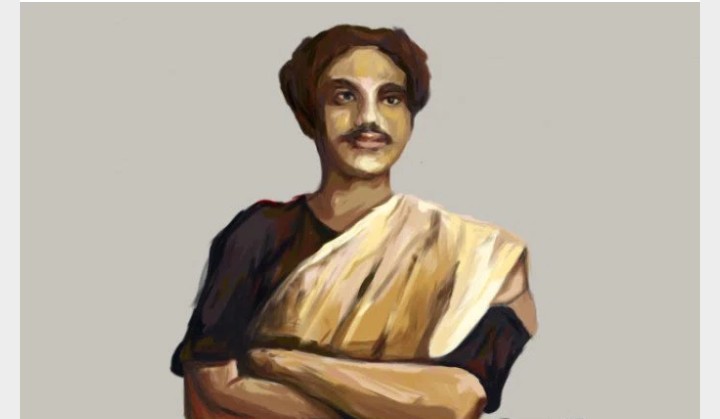
চলে এল আরেকটি নজরুল জয়ন্তী । আমাদের জাতীয় কবি, চির যৌবনের কবি, প্রেম এবং দ্রোহ যার লেখনীতে মিলেছে এক সুরে, সেই প্রাণের কবি কাজী নজরুল ইসলামের ১২৩ তম জন্মবার্ষিকী। কবির জন্মবার্ষিকীতে শ্রদ্ধা এবং ভালবাসা।
নজরুল এক অস্থির সময়ে বাঙালি মানষের প্রচণ্ড ক্ষোভের নাম। জন্ম তার দু:খ দারিদ্রে, অনাথ এতিম অবস্থায়। সেই শিশু কাল থেকেই তাকে ঘিরে ধরেছে দারিদ্রের অভিশাপ। দুবেলার দু মুঠো অন্ন জোগাড় করেছেন নিজের অর্জনে, যখন তার থাকার কথা খেলার মাঠে, শিশুদের পাঠশালায় স্লেট চক হাতে। তাই সব সময়ই দেখা যেত তার কাব্যে পরাজিতের জন্য, দূর্বলের জন্য, সর্বোপরি মানুষের জন্য সুতীব্র ভালবাসার কথা। নজরুল হয়ে উঠলেন গনমানুষের কণ্ঠস্বর। তার কবিতা গানে কিংবা যে কোন লেখায় প্রকাশ পেল সাম্যের কথা, অসাম্প্রদায়িক এবং বৈষম্যহীন এক সমাজের কথা। তাই তার ভরাট কণ্ঠে শোনা যায় সাম্যের অমর বাণী –
গাহি সাম্যের গান
মানুষের চেয়ে বড় কিছু নাই, নহে কিছু মহীয়ান।
নজরুল স্বাধীন চেতা। আজন্ম বিদ্রোহ যার রক্তে, তার কি ভাল লাগে বৃটিশরাজের এই ছড়ি ঘোরানো ?? সাধারণ প্রজাকূলের উপর অত্যাচারের খড়গ চালন ? তাই একটু বুঝতে শেখার পর থেকেই চাইতেন বৃটিশ বিতারণ । কিন্তু কেমন করে ? ভাবতে ভাবতেই শুরু হল বিশ্বযুদ্ধের ডামাডোল । নজরুল ভাবলেন এই সুযোগ। কাটা দিয়ে কাটা তোলবার মত করে তিনি বৃটিশদের হয়ে যুদ্ধের প্রশিক্ষণ নিয়ে, তাদেরই বিরুদ্ধে সে শিক্ষা কাজে লাগাবেন এমন ভাবলেন। সদ্য কৈশর উত্তীর্ণ নজরুল তখন উঠতি কবি। হাবিলদার হিসেবে সেনা বাহিনীতে যোগ দেয়ায় তিনি হলেন হাবিলদার কবি।
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হয়ে গেল নজরুলের প্রশিক্ষণ শেষ হবার আগেই । তাই আর যুদ্ধে যাওয়া হয় নি। কিন্তু যুদ্ধ তার মনে গভীর ভাবে রেখাপাত করে। তার ছাপ আমরা তার লেখনীতে হরদম দেখতে পাই পরবর্তী সময়ে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের স্মৃতি নিয়ে তিনি লিখলেন কামাল পাশা নামের সুদীর্ঘ কবিতা। এই কবিতায় তিনি আধুনিক তুরস্কের প্রতিষ্ঠাতা মোস্তফা কামাল পাশার স্তুতি রচণা করেছেন। নজরুল সব সময় স্বপ্ন দেখতেন একটি অসাম্প্রদায়িক এবং ভেদাভেদহীন সমাজ গঠনের । তাই খিলাফতের বহু যুগের একটা স্থবিরতা এবং পরিবারতন্ত্রের মুলোৎপাটোন কারী হিসেবে কামাল পাশাকে তিনি শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন।
হাবিলদারের চাকরি ছেড়ে কবি তখন পুরোদস্তর কবি। একরাতে তার চিত্তে কিসের যেন চঞ্চলতা। খুব দ্রুত চলে আসছে কবিতার লাইন। কলম বারবার দোয়াতে ডোবাতে হয় বলে পেন্সিলে লেখা হল এই দীর্ঘ কবিতাটি। যার প্রথম পাঠক কমরেড মুজাফফর আহমেদ, নজরুলের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। কবিতা পাঠেই তিনি বুঝলেন, সারা বাংলায় নজরুলের জন্য কি বিপুল খ্যাতি এবং বিড়ম্বনা হাত ধরাধরি করে অপেক্ষা করে আছে। বাংলা কাব্য ধারায় যুগের বদল ঘটানো কবিতা।
বল বীর
বল উন্নত মম শির।
শির নেহারি আমারি নত শির ওই শিখর হিমাদ্রির !
বল বীর।
কি বিদ্রোহ, কি দাউদাউ আগুন। যেন দীর্ঘদিনের ঘুমিয়ে থাকা জাতির জীবনে বারুদের আগুন হয়ে দেখা দিল কবিতাটি। আমি মানি নাকো কোন আইন, আমি টর্পেডো আমি ভীম ভাসমান মাইণ – বিদ্রোহী চিত্তের অসাধারণ প্রকাশ। কবিতাটির পত্রিকা প্রকাশ নিয়েও মজার ঘটনা আছে। কবিতাটি নজরুল নিয়ে যাচ্ছিলেন সে সময়ের জনপ্রিয় একটি পত্রিকায় প্রকাশের জন্য। কিন্তু মাঝপথে বিজলীর সম্পাদক তাকে দেখে থামান এবং কবিতা পড়েই বলেন, কালই আমার পত্রিকায় ছেপে দিচ্ছি।
১৯২২ সালে বিজলী পত্রিকায় কবিতাটি প্রকাশ পায় ।পরে অবশ্য মোসলেম ভারত পত্রিকায় কবিতাটি ছাপা হয় । এর পরে তো ইতিহাস । বললে অত্যুক্তি হবে না, এই একটি কবিতা নজরুলকে সর্ব ভারতীয় কবি হিসেবে পরিচিত করল এবং তিনি উপাধি পেলেন বিদ্রোহী কবি নামে।
নজরুল এর কিছুদিন পরে ধুমকেতু নামে পত্রিকা বের করলেন । সেখানে জ্বলত কলমের আগুন, বিক্ষোভের তপ্ত ঝাজ গিয়ে লাগত বৃটিশরাজের গায়ে । প্রলয়োল্লাস, আনন্দময়ীর আগমনে, আগমনী, ধুমকেতু, শাত-ইল্-আরব, আবার তোরা মানুষ হ ইত্যাদি আরো অসংখ্য রক্তগরম কবিতা । এগুলো বাংলা কবিতার মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছিল এবং একটা নব চেতনার সৃষ্টি করল । যার প্রভাব পরবর্তী অনেক কবির কবিতায় লক্ষ্য করা যায় ।
নজরুল ছিলেন মনে প্রাণে বিদ্রোহী । লেখনিতে বিদ্রোহ আনা হয়ত অনেকের পক্ষেই সম্ভব কিন্তু মনের জোর না তাকলে তা বেশিদিন টেকে না । নজরুল তার কবিতার মাধ্যমে যে তীব্র প্রতিবাদের জোয়ার তুলেছিলেন, তা থামাবার জন্য জেলে পুরে তাকে দমাতে চেয়েছিল ইংরেজ সরকার । নজরুলের পূর্বেও বেশ কিছু বঙ্গকবির ভাগ্যে রাজরোষ জুটেছিল কিন্তু নজরুলের মত এত তীব্রভাবে কাউকে আক্রমন করা হয়নি । অগ্নিবীণা (য়েখানে বিদ্রোহী সহ আরো বেশ কিছু বিখ্যাত কবিতা ছিল) কাব্যগ্রন্থটি ১৯২২ সালে প্রকাশিত হয় এবং প্রকাশরে কিছুকাল পরেই এটি বাজেয়াপ্ত করা হয় । ১৯২২ সালেই কবির বিথ্যাত কবিতা আনন্দময়ীর আগমেনে প্রকাশিত হয় যা ছিল ইংরেজ রাজশক্তির জন্য চপেটাঘাত স্বরূপ । জবাব দিতে তারা মোটেই দেরি করেনি । কিছুদিনের মধ্যেই তারা হানা দেয় ধূমকেতু অফিসে, কবির বাড়িতে । কবিকে কলকাতা থেকে পালিয়ে আসতে হয় ।
১৯২৩ সালে কবিকে গ্রেফতার করা হয় কুমিল্লা থেকে । নজরুলের পক্ষ সমর্থনে বেশ কজন আইনজীবী বিনা পারিশ্রমিকে এগিয়ে এসেছিলেন । তাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন মলিন মুখোপাধ্যায়। যাই হোক বিচারক সুইনহো (সে নিজে একজন কবি ছিল) নজরুলকে সাধারণ কয়েদীদের মত এক বছর সশ্রম কারাদন্ড দেয় । নজরুল আদালতে যে জবানবন্দী দেন তা রাজবন্দীর জবানবন্দী নামে খ্যাত বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে । কারাগারেবন্দীদের সাথে নির্যাতন মূলক আচরণ, বৈষম্য এবং রাজবন্দী হিসেবে প্রাপ্য মর্যাদা না দেয়ায় তিনি অনশন শুরু করেন ।
সারা ভারতবর্ষ জুড়ে তুমুল আলড়ন তোলে ঘটনাটি । বাংলার সাহিত্যসমাজ ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে । প্রখ্যাত ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় স্বয়ং এসে নজরুল কে অনুরোধ করেন অনশণ ভাঙতে । যদিও শরৎবাবু জেলগেটে নজরুলের দেখা পাননি । বিশ্বকবি ভারতরবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অনশন ভাঙার অনুরোধ করে তার বার্তায় জানান, গিভ আপ হাঙ্গার স্ট্রাইক, আওয়ার লিটারেচার ক্লেইমস ইউ। কবি তখন শিলং এ ছিলেন । বিচিত্র কোন কারণে সে তার বার্তা ফেরত যায় অর্থাৎ নজরুলকে জানানো যায় নি । কবির কারাবাসের মাঝেই কবিগুরু ১৯২৩ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি নজরুলকে তার বসন্ত নাটক টি উৎসর্গ করেন । দ্রোহের কবি নজরুল তখন আলীপুর সেন্ট্রাল জেলে । উৎসর্গ পত্রে উৎকীর্ণ হয়- উৎসর্গ, শ্রীমান কবি নজরুল ইসলাম স্নেহভাজনেষু, ১০ ফাল্গুন ১৩২৯ বঙ্গাব্দ ।
নজরুলের বিরোধী মহল একে রবি ঠাকুরের মতিভ্রম বলে উল্লেখ করে । অনেকেই হাবিলদার কবিকে স্বীকৃত দিতে চায় না কবি বলে । কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তাদের কথা অগ্রাহ্য করেন । বসন্ত গ্রন্থখানি নজরুলকে দেবার জন্য পবিত্র বাবুর হাতে একটি কপি তুলে দিয়ে কবি বলেন, “জাতির জীবনে বসন্ত এনেছে নজরুল। তাই আমার সদ্য প্রকাশিত ‘বসন্ত’-গীতিনাট্যখানি ওকেই উৎসর্গ করেছি। সেখানা নিজের হাতে তাকে দিতে পারলে খুশি হতাম, কিন্তু আমি যখন নিজে গিয়ে দিয়ে আসতে পারছি না, ভেবে দেখলাম, তোমার হাত দিয়ে পাঠানোই সবচেয়ে ভালো, আমার হয়েই তুমি বইখানা ওকে দিও।” তিনি আরো বলেন, ‘তাকে বলো, আমি নিজের হাতে তাকে দিতে পারলাম না বলে সে যেন দুঃখ না করে। আমি তাকে সমগ্র অন্তর দিয়ে অকুণ্ঠ আশীর্বাদ জানাচ্ছি। আর বলো, কবিতা লেখা যেন কোন কারণেই সে বন্ধ না করে। সৈনিক অনেক মিলবে কিন্তু যুদ্ধে প্রেরণা জাগাবার কবিও তো চাই”’ এত বোঝা যায় নজরুলের প্রতি রবি বাবুর গভীর অনুভূতির কথা ।
দারুন অস্বস্তিতে পড়ে অবশেষে ব্রিটিশরা রণে ভঙ্গ দেয় । দাবি মেনে নেয়ার আশ্বাস দেয়া হলে শেষ পর্যন্ত কবির মাতৃস্থানীয়া বিরজাসুন্দরীর অনুরোধে ৩৯ দিন অনশন থাকার পর ২২ শে মে ১৯২৩ সালে নজরুল তাঁর অনশন ভঙ্গ করেন । কি অদম্য মনোবল । খুব কম লোকের পক্ষেই এটা সম্ভব ।
যাই হোক আজন্ম বঞ্চনা এবং শোষণের বিরুদ্ধে লড়াই করে আসা নজরুলের চেতনা এবং তার সাহিত্যকর্ম আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধের প্রেরণা হয়েছিল । কি বিষ্ময়কর উচ্চারণ
কারার ওই লৌহ কপাট
ভেঙে ফেল কর রে লোপাট
রক্ত জমাট, শীতল পুজোর
পাষাণ বেদি ।
কবি নজরুল যে শুধু দ্রোহের কবি ছিলেন, তাই নয় তার কাব্যে প্রেমের রূপ মূর্ত হয়ে উঠেছে বিচিত্রমাত্রায় । আমরা সবাই জানি নজরুল ইসলাম একজন অত্যন্ত প্রতিভাধর এবং অত্যন্ত স্বল্প সময়ের জন্যে রাজত্ব করা কবি । যেন হঠাৎ ধুমকেতুর মতই তার আগমন আবার ওরই মতন মিলিয়ে যাওয়া । মোটামুটি ১৯২০ থেকে ১৯৪০ সাল পর্যন্ত নজরুলের সাহিত্য চর্চার সময়কাল হিসেবে ধরা যায় । ভাবলে অবাক হতে হয় মাত্র বিশ বছরে কবির কি বিপুল এবং বহুমাত্রিক সৃষ্টি । কাব্য সাহিত্য, উপন্যাস, নাটক, প্রবন্ধ, কথিকা, সঙ্গীত, গীতিনাট্য, সুর সৃষ্টি, আবৃত্তি, চলচ্চিত্রে সঙ্গীত পরিচালনা কিংবা অভিনয় , যেখানেই হাত দিয়েছেন সে খানেই সোনা ফলেছে । তাই নজরুল সাহিত্য সম্ভার নিয়ে আলোচনা খুব কিঠন একটা কাজ ।
অনেকটা সময় ধরে মানুষ এবং সাহিত্যিক নজরুলরে বিদ্রোহী চেতনার বহিপ্রকাশ নিয়ে আলোচনা হল । এবারে নজরুল সাহিত্যে প্রেমের প্রকাশ এবং তার বহুমুখী মাত্রা নিয়ে আলোচনা করা যাক ।
নজরুল নিজেই বলেছেন,
মম এক হাতে বাকা বাশের বাশরী
আর হাতে রণতূর্য ।
সত্যিই তাই । নজরুল সাহিত্যধারায় দ্রোহের পাশাপাশি প্রেমের অপূর্ব সম্মিলন ঘটেছে । তাই শোনা যায় প্রেয়সীর কণ্ঠের ব্যাকুল আকুতি-
দেবতাগো ফিরে চাও
মোর বেদনার তপস্যা শেষ
মিলনের বর দাও ।
কিংবা আরেক জায়গায় কবি বিরহকাতর প্রেমিকের কণ্ঠ বলে ওঠেন,
তুমি সুন্দর তাই চেয়ে থাকি প্রিয়
একি মোর অপরাধ ??
অথবা পূজারিণী কবিতায় শুনি কবির ভিন্নধর্মী উচ্চারণ-
…আমি তোমায় জন্মে জন্মে চিনি ।
পূজারিণী ।
ঐ কণ্ঠ, ও কপোত কাদানো রাগিণী
ঐ আখি, ঐ মুখ
ঐ ভুরু , ললাট, চিবুক
ঐ তব অপরূপ রূপ
ঐ তব দোলো- দোলো, গতি-নৃত্য দুষ্ট দুল রাজহংসী জিনি’-
চিনি সব চিনি ।
এই যে প্রেমের আকুতি সে কোন বড় যোদ্ধার নয়, বড় বিপ্লবীর নয়, নয় কোন গৃহত্যাগী সন্যাসীর । এ একান্তই একজন সাধারণের, যার হৃদয়ের অনুভূতি প্রকাশ আমাদের বাধ্য করে সহানুভূতি নিয়ে এগিয়ে যেতে ।
নজরুলের কাব্যে এবং গানে বহুমাত্রিকতার আরেকটি দিক হচ্ছে পারিভাষিক এবং বিদেশী শব্দের ব্যাবহার । দু একটি উদাহরণ দেয়া যাক । যেমন শাত-ইল আরব কবিতায়
কুত- আমারার রক্তে ভরিয়া
দজলা এনেছে লোহুর দরিয়া ।
আবার কোরবানী কবিতায়-
খঞ্জর মারো গর্দানেই
পঞ্জরে আজি দরদ্ নেই
মর্দানীই পর্দা নেই
ডরতা নেই আজ খুন-খারাবীতে রক্তলুব্ধ মন ।
এতো গেল কাব্যে বিভাষার ব্যাবহার । এই গানটিতে খেয়াল করুন, কি নিপুন ব্যাবহার ঘটেছে এই গানটিতে
আলগা কর গো খোপার বাধন
দিল বহি মেরা, ফাস গায়ি ।
কানেরো দুলে প্রাণ রাখিলে বিধিয়া
আখ ফেরা দিয়া , চোরি কার নে দিয়া
দেহেরো দেউড়িতে বেড়াতে আসিয়া
অর নেহি ভো বাপাস গায়ি ।
কি চমৎকার সম্মিলন । বাংলা কাব্যে এবং গীত রচনায় ভিন্নভাষার শব্দ এবং পরিভাষার এমন সার্থক ব্যাবহার নজরুল ব্যাতীত আর কারো হাতে হয়নি । সেদিক থেকে নজরুল ইসলাম একে বারেই অপ্রতিদ্বন্দ্বী ।
একই শ্বদ ভিন্ন ভিন্ন অর্থে ব্যবহার এবং ধ্বনি-ব্যাঞ্জনা সৃষ্টিতে নজরুলের দক্ষতা ছিল তুলনাহীন । মোহররম কবিতায় ব্যবহৃত “লাল” শব্দ তার উদাহরণ ।
নীল সিয়া আসমান, লালে লাল দুনিয়া-
আম্মা, লাল তেরি খুন কিয়া দুনিয়া ।
এই স্বল্প পরিসরের লেখায় নজরুলের আরো বেশ কিছু সাহিত্যকর্মের দিক আলোচনা করা গেল না । আসলে সম্ভব নয় এত বড় মাপের কবির জীবন দর্শন এত ছোট্ট লেখায় তুলে ধরা সম্ভব নয়। এবারে নজরুল প্রসঙ্গে একান্তই আমার সাধারণ কিছু অভিমত ।
নজরুল এখনো অনাবিষ্কৃত কবির নাম । তার রচনার বিপুল সম্ভার সম্পকে আমাদের ধারণা এখনো পরিষ্কার নয় । আমরা তার সাহিত্যকর্মের অনেক দিকই জানি না । এবং বাংলা সাহিত্যে অন্যান্য অনেক কবির থেকে নজরুলকে নিয়ে অপপ্রচার এবং সমালোচনা হয়েছে বেশি এবং উদ্দেশ্য প্রণোদীত ভাবে । যা একদমই অনুচিত কাজ ছিল । কবি নজরুল শ্যামা সঙ্গীত , হরিনাম, কীর্তন রচনা করেছেন তাই তিনি হয়েছেন কাফের, হিন্দুত্ববাদী -আবার গজল ইসলামী সঙ্গীত রচনা করেছেন, আরবী ফারসী সাহিত্যকর্ম বাংলায় অনুবাদ করেছেন, কবিতা গানে বা সাহিত্য কর্মে ফারসী আরবী হরদম ব্যবহারে সিদ্ধ ছিলেন তাই গোড়াপন্থীদের কাছে ছিলেন সাম্প্রদায়িক । অথচ কবি সে যুগে প্রমীলা দেবীকে বিয়ে করেছেন যিনি কিনা একজন হিন্দু ছিলেন । তার হাত ধরে মুসলমানের অন্দরে গেছে বাংলা গান
ও মন রমজানের ওই রোজার শেষে
এল খুশির ঈদ ।
আমরা জানি, সশিক্ষায় যারা শিক্ষিত, তাদের কিবা দরকার প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার ?? রবীন্দ্রনাথ নজরুল এরা অন্য স্তরের কবি । প্রকৃতি এদের শিক্ষক । গৎবাধা নিয়মের বিষমাবর্তে এরা কখনোই বাধা পড়েন নি । তাই কবি ইংরেজী ভাষায় বিশেস কোন শিক্ষা লাভ না করেও তৎকালীন ইউরোপীয় সাহিত্য সম্পর্কে সম্যক ধারণা রাখতেন যার প্রমাণ পাওয়া যায় শান্তিপদ সিংহের বইতে ( বর্তমান বিশ্বসাহিত্য) । এখানে তিনি নিজের এবং কবির মধ্যে ইংরেজী পুস্তক পঠন নিয়ে বলছেন,
‘একদিন কবি বললেন, কইরে, আর বই আনছিস না কেন ? বললাম- এই ক’মাস ধরে যা খেয়েছ তা হজম কর । কবি বেশ ক্ষুণ্ন হলেন । আমি তখন সত্য বললাম যে তেমন বই আমাদের লাইব্রেরিতে নেই।
নজরুলের পাঠাভ্যাসের এ বিবরণের সত্যতা কিন্তু তার সারা জীবনের সমস্ত সাহিত্য কমেই আছে । যেমন বিদ্রোহী কবিতাতেই কবি বলেছেন গ্রীক মিথের উপমার কথা । যেখানে একই সাথে হাত ধরাধরি করেছিল গ্রীক এবং ভারতীয় পুরান । শিবের গাজনের সাথেছিল অর্ফিয়াসের বাশরী । এরূপ শত প্রমাণ সত্বেও আমাদের কাছে গুরুত্ব পায় সুশীল কুমার গুপ্তের কথা-
” মোহিতলাল বুদ্ধির বিবর্ধনের জন্য নজরুলকে ব্রাউনিং, কীটস, শেলী বা বায়রণ পড়তে বলতেন । কিন্তুনজরুল এসব পড়তে চাইতেন না । শেলীর কিছু কবিতা পাঠ ছাড়া অন্য কবিদের লেখা তিনি প্রায়ই পড়তেনই না বলা চলে ”
এরকম অসংখ্য অপপ্রচার হয়ে আসছে নজরুলকে নিয়ে । আমাদের সময় এসছে সাম্যেরে কবি, মজলুমের কবি, গনমানুষের কবি নজরুলকে নতুনভাবে চেনার, নতুন করে জানার ।
আশা করি আমার একান্ত অনুভূতি গুলো আপনাদের ভাল লাগল । এবারে নজরুলের চরণতলে আমার কবিতার অর্ঘ্য । কবিতার নাম নতুনের গান ।
নতুনের গান
পুরাতন পৃথিবী বলরে তুই বল
পুরানের শৃংখল
ভাঙবি কবে তুই
আধারের ভুই
করবি কবে দূর
নতুনের গানে তুলবি কবে সুর
কতকাল আর- বুড়োদের মরা গান
গেয়ে যাবি
করবি
জীবন সারা
থাকবি কী রে যৌবনেতে মরা
অমৃতের ওই সোনার পেয়ালা খান
রাখবি বিষে ভরা ?
ওরে অবোধ, হবে কী চেতন তোর ?
আসবে মনে কী দীঘল রাতের ভোর ??
হতভাগা ওরে, জাগরে আজকে জাগ
নতুনের মাঝে
নেরে আসন, কর নিজেরে ভাগ
সকাল সাঝে
দুপুর রাতে কর নতুনের গান
তোল জীবনের উদ্দ্যম তান
বল নবীনের গান-নবীনের প্রাণ
শক্তি তার চির অফুরাণ ।
গানে গানে তোল মহাবিদ্রোহের সুর
হয়ে ওঠ স্বর্গ, মর্ত্য গগন বিদারী
অমর মহিষাসুর ।
মদমত্ততার পাত্র কররে চুর !
তাতে ঢাল প্রাণের অমিয়বারি ।
জেগে ওঠ, হয়ে তেজদীপ্ত তেজক্রিয় কণা
তোল পদ্ম গোখরোর ফণা,
দে তোর আপন হাতে
এই কৃষ্ণ ঘন রাতে,
শোষকের গদি নেড়ে !
হে আজ হুমকির মারণ গোলা ছেড়ে ।
বল হুংকারে, আমি মানুষ, চাই
মানব অধিকার, আর কিছু নাই
আমায় থামাবার
আমি দূর্বার, অটল, গিরিধার ।
হয়ে ওঠ তুই, দারুন মাতৃময়ী
জগত আনন্দময়ী
দে দূর্বল চিত্তে, বঞ্চিতের প্রাণে,
নিপীড়নের করুন রোদনে
একটু সাহস
একটু আদর, একটু স্নেহের পরশ !
জানবি জীবন, বহু রঙ তার প্রাণে
বেদনায় যে আনন্দ, সেও জাগে রাগ ইমনে ।
জেগে ওঠ ওরে পরাজিত মানবতা
তুলে নে অস্ত্র যত লাঙল, কলম কিংবা খাতা
লেখ ফসলের মাঠে
নদীর ঘাটে
জীবনের জয়গাঁথা ।
সে রূপ কণ্ঠে তোল, ওহে ধরিত্রীমাতা ।
তবেই বলব তোরে-
আমার গলা ছেড়ে,
তুই অজর, অমর অক্ষয়
কোন নরকের ক্রোধানলে তুই ধ্বংস হবার নয় ।